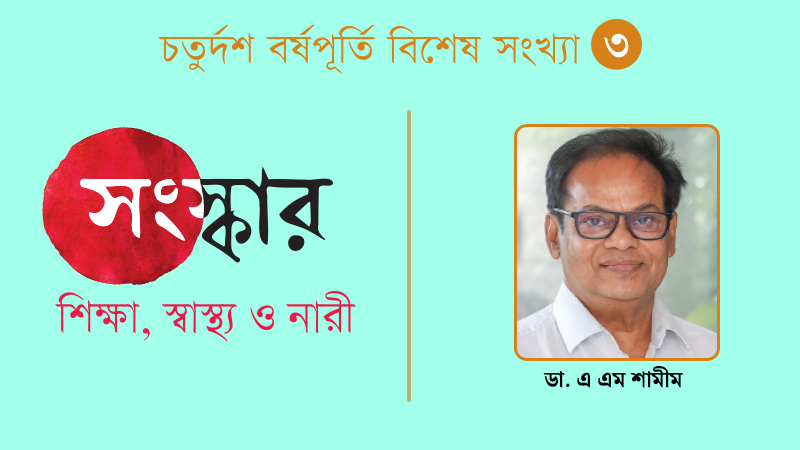দেশে চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। সবার প্রত্যাশা ছিল, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এ খাতে বড় সংস্কার হবে। গত এক বছরে স্বাস্থ্য খাতে কতটা পরিবর্তন দেখতে পেলেন?
আগে প্রচুর দুর্নীতি হতো। ধরেন, ২০০ কোটি টাকার কেনাকাটা হলো। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এল না। কভিডের সময় ভ্যাকসিন কিনতে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার মতো খরচ হলো। কিন্তু ওই ভ্যাকসিন বানানোর সক্ষমতা বাংলাদেশেই ছিল। একটা কোম্পানি ওটা বানিয়েও ফেলেছিল। কিন্তু একটা বিশেষ গ্রুপের সুবিধার জন্য সব ভ্যাকসিন বিদেশ থেকে কেনা হলো। এটা দুর্নীতি। যেকোনো কাজের সময় ক্ষমতায় থাকা লোকজন চিন্তা করতেন যে এতে তারা সুবিধাভোগী হবেন কিনা। গত এক বছরে কিন্তু আমরা এমনটা দেখিনি। এখন আমাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এ মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক দিন কাজ করছেন। উনারা একসঙ্গে কাজ করছেন। এতে দুর্নীতিমুক্ত একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। তবে এ সময়ে হয়তো নতুন অনেক কিছু যুক্ত হয়নি।
আপনি অনেক দিন ধরে স্বাস্থ্য খাতে যুক্ত রয়েছেন। এ খাতে কোন কোন জায়গায় সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন?
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটা বড় বিষয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য, সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য, টারশিয়ারি স্বাস্থ্যসেবা (জটিল, বিশেষায়িত ও উন্নত চিকিৎসা), তারপর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও—সব নিয়েই কিন্তু স্বাস্থ্য খাত। আমরা প্রাইভেট হেলথকেয়ার নিয়ে কাজ করি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের একটা প্রোগ্রামে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেছেন যে তারা বেসরকারি খাতকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। সরকারি হাসপাতালে মাটিতে শুয়ে থাকলে বা ডাক্তার না পেলে অতটা সমালোচনা হয় না, যেটা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হয়। তার মানে, বেসরকারি ও সরকারি ব্যবস্থাপনা পাশাপাশি চলবে। এটা একটা বড় ব্যাপার।
দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে উনারা (সরকার) আমাদের যুক্ত করতে চান। তারা বলছেন, হসপিটাল রেগুলেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সেবা বৃদ্ধিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা নিয়ন্ত্রণ বডিতে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাজ করা মানুষদের আনতে চান। এটা বেশ ভালো পদক্ষেপ।
খুব সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় বলি। প্রথম হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য। নিউট্রিশন কোত্থেকে আসবে, ধূমপান বা মাদকদ্রব্যকে না বলা, শিশুর যে মায়ের দুধ খাওয়াটা জরুরি সেটা বলা, ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবে আমাদের কী করণীয়—এসব বিষয়। এখানে আগে আসবে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা। আমরা সাধারণত বেসরকারি ব্যবস্থাপনা বলতে হায়ার সেকেন্ডারি সমস্যা, যেমন কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল, হার্ট অ্যাটাক করল, বাইপাস সার্জারি, সিজারিয়ান, হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি—এগুলোকে বলে থাকি। কিন্তু এগুলো মোট সেবা গ্রহণকারীর পাঁচ ভাগ মাত্র। ৮০ শতাংশ মানুষ জ্বর বা পেট খারাপ হলে কোয়াক (হাতুড়ে) ডাক্তারের কাছে কিংবা ফার্মেসিতে যান। তখন ননকোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্টরা একটা ওষুধ দিয়ে দেয়। সুতরাং এ ধরনের রোগীর জন্য এনজিও, সরকারি ও বেসরকারি—এ তিন বডিকে একসঙ্গে আসতে হবে। আমাদের দেশে ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। এগুলোর কিন্তু এখন কাজ নেই। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর একবার শুনলাম, এগুলোর নাম হবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এগুলো এখনো ভালো ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নেই। এ প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাকটিভ করতে হবে। আমরা ১৫ হাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে যদি বাংলাদেশের প্রাইমারি হেলথকেয়ারের অধীনে এনে এখানে ৯০ শতাংশ সার্ভিস দিতে পারি, তাহলে মানুষের যে মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্য, তার বড় অংশটাই পূরণ হবে।
আরেকটা বিষয় বলা প্রয়োজন। পরিবার-পরিকল্পনায় প্রায় ৪৫ হাজার কর্মী কাজ করেন। এখন পরিবার-পরিকল্পনার উপকরণ অনেক কম আসে। আগে প্রচুর পিল দেখতাম, কনডম দেখতাম। মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে অনেক কিছু হতো—সন্তান কমানো, এক সন্তান বা দুই সন্তান ভালো—এমন প্রচারণা টিভিতে দেখা যেত। এখন এগুলো নেই। কারণ ওদের বাজেট কমে গেছে। এ ৪৫ হাজার লোকবল কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য খাতের কাজে ব্যবহার করতে পারি। ৪৫ হাজার সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বড়। কিন্তু আমরা সব সময় শুনি—ডাক্তার নাই, নার্স নাই। পরিবার-পরিকল্পনার জনবল কাজে লাগানো যায়। ১৫ হাজার স্বাস্থ্য ক্লিনিককে কাজে লাগানো যায়। তাহলে জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।
আমাদের এনআইডি কার্ডের সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য যুক্ত করা যায়। একজন ডাক্তার একটা রোগীকে ৫-৭ মিনিট দেখেন। এর মধ্যে ৪ মিনিট লাগে তার কাগজগুলো গোছাতে। একদম ফরজ কাজ হলো—আমাদের এনআইডির সঙ্গে মেডিকেল সামারি থাকতে হবে। এনআইডিটা কিন্তু আমাদের খুব মানসম্পন্ন। আপনি এনআইডি দিয়ে অনেক কিছু খুলে ফেলতে পারেন। এর সঙ্গে কিন্তু মেডিকেল সামারিটা খোলা কোনো কঠিন কাজ নয়।
দেশে প্রাইভেট হাসপাতালের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এগুলোর সেবার মান ঠিক রাখতে সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
বাংলাদেশে ১৫ হাজার হসপিটাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ১২ লাখ লোক কাজ করেন। ১২ লাখ লোক ১৪ কোটি মানুষকে সেবা দেন। এর মধ্যে ৬৫-৭০ শতাংশ রোগী পকেট থেকে তার মোট খরচের ৭০ শতাংশ দেন।
অর্থাৎ, প্রাইভেট হেলথকেয়ারের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে ১৮টি লাইসেন্স লাগে। এ মুহূর্তে ১৫ হাজার হসপিটাল ও ডায়াগনস্টিকের যে লাইসেন্স আছে এদের মধ্যে নয় হাজারের নবায়ন হচ্ছে না। কারণ পরিবেশগত লাইসেন্স নেই। ফায়ার লাইসেন্স না থাকায় আরো দুই হাজারের কাগজপত্র নবায়ন হচ্ছে না। একটা লোকের যদি একটা জায়গায় তিনদিনও যাওয়া লাগে, তাহলেও তো ১০০ লোক লাগে। এসব বিষয়কে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা দরকার। আমরা একটা লাইসেন্সের জন্য ১ লাখ টাকা দিই। তার মানে, ১৫ হাজার থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা আসে। এক ছাতার নিচে আনা হলে একজন মহাপরিচালক থাকবেন, পরিবেশ, ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এখানে যুক্ত থাকবেন। তাহলে আমাদের ভোগান্তিটা কমে যাবে। একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আমরা সহজে সব কাগজপত্র পেয়ে যাব।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো—এক. আমাদের এনআইডির সঙ্গে মেডিকেল সামারি। দুই. সব কমিউনিটি ক্লিনিক যুক্ত করা। তিন. পরিবার-পরিকল্পনার ৪৫ হাজার জনবলকে কাজে লাগানো, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে একীভূত করা। চার. পাবলিক-প্রাইভেট ও এনজিওকে এক ছাতার নিচে এনে তিনটি শাখার মতো কাজ করা। পাঁচ. বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারের ১৮টি লাইসেন্সকে এক ছাদের নিচ থেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা।
সংস্কারের জন্য দুই হাজার পৃষ্ঠার বইয়ের দরকার নেই। সংস্কারের ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ এসে পড়বে অ্যাপের মাধ্যমে। আর দরকার পড়াশোনা জানা অভিজ্ঞ ভালো নেতৃত্ব সামনে নিয়ে আসা। দলীয়করণ না করা।
বাইরের দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের হাসপাতালের কী কী পার্থক্য দেখতে পান। এক্ষেত্রে আমাদের আর কী কী উন্নতি প্রয়োজন?
বিদেশের হাসপাতালে বেশকিছু জিনিস লক্ষ করা যায়। একটি হলো, হাসপাতালের অবকাঠামো, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আরেকটি হলো, ওখানে মানুষ খুব পরিচ্ছন্ন। রোগীর এত ভিড় থাকে না। সুন্দর করে কথা বলে। বসার চেয়ারটা ভালো। ওসব দেশে রোগীদের ডাটা সংরক্ষণ একদম আমাদের দেশের মতো। বিদেশের ডাক্তাররা আমাদের ডাক্তারদের মতোই রোগী দেখেন। কিন্তু তারা দেখেন ১৫ মিনিট। আমাদের দেশে তা ৫ মিনিট।
বাংলাদেশের ১০০টি ডায়াগনস্টিকের রিপোর্ট—ল্যাবএইডের রিপোর্ট—সিঙ্গাপুর-ব্যাংককে নেয়া হলে রিপিট করায় না। হার্টের বাইপাস সার্জারি উন্নত দেশের হাসপাতালের চেয়ে বাংলাদেশে কম খরচে করা যায়। আমরা কোনো রোগীকে বাইরের দেশে গিয়ে চিকিৎসা নেয়ার জন্য বলি না। আমাদের হাসপাতালেই বাইরের দেশের চিকিৎসার সবকিছু রয়েছে।
আমাদের দেশে নাক সিটকানোর একটা ব্যাপার রয়েছে। এ দেশের ডাক্তার খারাপ, সাংবাদিক খারাপ, বাতাস খারাপ। এ রকম চিন্তা ঢুকে গেছে। এ পরিস্থিতি তো একদিনে পরিবর্তন করা সম্ভব না। তবে স্বাস্থ্য খাতের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। শুধু একটা ফাইন টিউনিং দরকার।
আমাদের কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন আমাদের ব্যাংক সুদের হার অনেক বেশি। ধরেন, একটা ক্যান্সার হাসপাতাল করতে সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি। আরো ৫০ কোটি টাকা লাগবে। এটার জন্য অনেক ইন্টারেস্ট আসে! অথচ সরকারের অনেক খাত আছে যেখানে আরো কম সুদে ঋণ দেয়া হয়। চিকিৎসা নিতে বিদেশগামীদের অনেককে এখন আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি। অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাচ্ছি। এক বছর ধরে ভারত ভিসা দিচ্ছে না। কোথাও শুনেছেন, ইন্ডিয়ায় যেতে না পারার কারণে কেউ মারা গেছেন! আগে যারা ভারতে যেত তারা এখন দেশে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। এসব বিবেচনা করে, হাসপাতালের জন্য যদি ইন্টারেস্ট (সুদ) কমিয়ে দেয়া হয়, তাহলে উপকার হবে। যারা মাঠে কাজ করেন তাদের সঙ্গে পলিসিমেকাররা কখনো আলাপ করেন না। ওনারা ওনাদের মতো করে কাজ করেন।
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার রোগীদের বোঝাতে হয়, মেশিন বসাতে সময় লাগে। বিনিয়োগের রিটার্ন আসতে সময় লাগবে। একটা হাসপাতালে প্রফিট আসতে সময় লাগে ছয় বছর। ওই সময়টা তো দিতে হবে। নইলে আমাদের দেশে শিল্প হবে না। গত পাঁচ বছরে কোনো বড় হাসপাতাল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা হয়নি। নতুন করে কেউ করবেও না। কারণ মানুষ মনে করে যে অন্যকিছুতে বিনিয়োগ করলে সমাজে কোনো বদনাম নেই, লাভও বেশি এবং চুপি চুপি অনেক কিছু করা যায়। করপোরেটরা আগে হাসপাতালে বিনিয়োগ করতে আসত। এখন আসে না। যারা একটা হাসপাতাল নির্মাণ করেছে তারা অন্য কোনো হাসপাতাল নির্মাণে যায় না। কারণ এটা ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা বিদেশে যাব না বলি, নিজের চিকিৎসা নিজে দেব বলি। কিন্তু এসবের জন্য নীতিনির্ধারকদের ফাইন্যান্সিং, লাইসেন্সিং, মনিটরিং, ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রামটা জনবান্ধব করতে হবে।
ল্যাবএইড হাসপাতাল নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
আমাদের যাত্র শুরু ১৯৮৯ সালে। এরপরে হাসপাতালে অনেক কিছু সংযোগ করেছি। ৩৬০ ডিগ্রি সার্ভিস যেটাকে বলা হয়। আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালসে সাত হাজারের বেশি মানুষ কাজ করে। আমরা আরো ভালো ওষুধ তৈরি করতে চাই। ক্যান্সার হাসপাতালকে আরো বড় করতে চাই। সেটা নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিডনি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। আমরা একটা কিডনি হাসপাতাল নির্মাণ করব। এরপর মা ও শিশুদের স্পেশাল কেয়ারের জন্য একটা হাসপাতাল দরকার। সারা বাংলাদেশে আরো দশটা হাসপাতাল নির্মাণ করতে চাই। উত্তরা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে কাজ শুরু করেছি। সমাজের সবার চিকিৎসাসেবা যেন নিশ্চিত করা যায়। আমরা সব জেলায় যাব। ল্যাবএইড যেসব জায়গায় গিয়েছে সেখানে গুণগত মান নিশ্চিত করেছে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, থেমে নেই। আমরা ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করেছি। সরকারেরও ফার্মেসির ক্ষেত্রে সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কার দীর্ঘমেয়াদি কিন্তু আমরা শুরু করেছি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর সবার আস্থা রাখা উচিত।